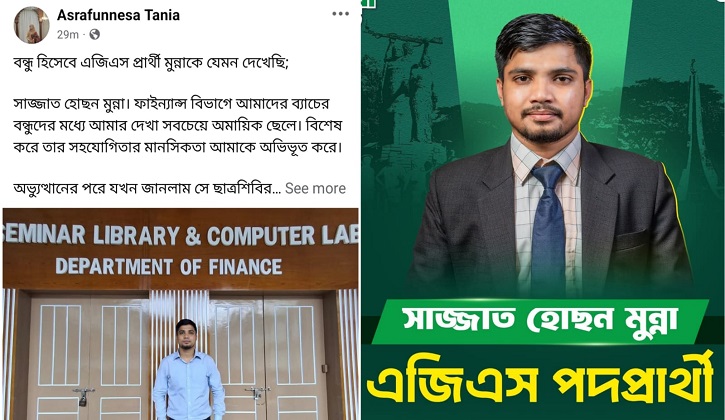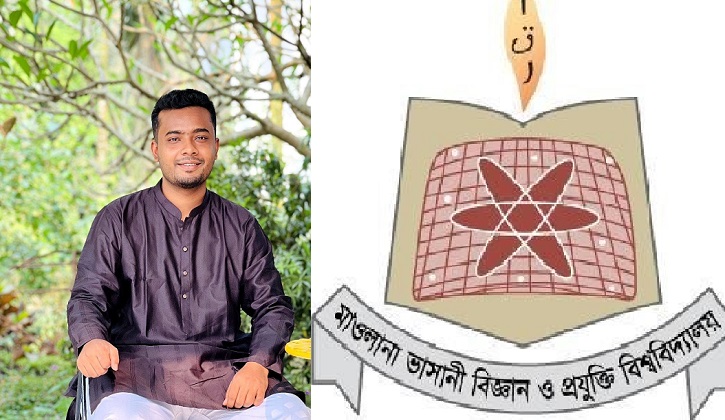পণ্য আমদানিতে ভারতের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল বাংলাদেশ। কোনো নিত্যপণ্যে ভারত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দিলেই বাংলাদেশে তার প্রভাব পড়ে। গত ডিসেম্বরে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার পর থেকেই অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে দেশের পেঁয়াজের বাজার। এর মধ্যে দাম কখনোই প্রতি কেজি ৮০ টাকার নিচে নামেনি, ১৫০ টাকাও ছাড়িয়েছে কয়েকবার।
তথ্য বলছে, আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজের মৌসুম শেষ হয়, ডিসেম্বরে হালি পেঁয়াজ ওঠা পর্যন্ত বাজারে টান থাকে পণ্যটির। বছরের এই সময়ে পেঁয়াজের বাজারে এরকম পরিস্থিতি ২০১৯ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই হয়ে আসছে বাংলাদেশে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের বাজারে বাড়তে থাকে দাম, যা গত নভেম্বর মাসে কেজিপ্রতি ২৫০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।
ব্যবসায়ী, কৃষি ও বাজার বিশেষজ্ঞ এবং ভোক্তা অধিকার বলছে, পেঁয়াজ সংকট কাটাতে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেয়ে ভালো কোনো উপায় নেই। পেঁয়াজের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান প্রয়োজন, যা আছে তা বিতর্কিত। এজন্য প্রয়োজনীয় এই নিত্যপণ্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা দরকার।
পাশাপাশি তারা বলছেন, ভারত বাদে বিকল্প দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির বাজার সৃষ্টি করতে হবে। বাজারে সিন্ডিকেট ও মনোপলি ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। কারণ প্রতি বছর ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সুযোগ কাজে লাগায় দেশি ব্যবসায়ীদের একটি অংশ। প্রকৃতপক্ষে যেটুকু সংকট তৈরি হয়, তার চেয়ে বেশি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়া পেঁয়াজ খাওয়ার পরিমাণ কমানোও সংকট মোকাবিলার একটি পথ হতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা।
দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। এটি একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর দাম বাড়লে বিষয়টি সামনে আসে, কিন্তু এখনো তা স্পষ্ট হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেয়। আর চাহিদার যে তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেয়, ব্যবসায়ীরা বলেন সেটি অনেক কম।
বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে পেঁয়াজের উৎপাদন ২৫ থেকে ২৬ লাখ টনের মধ্যে থাকে। অন্যদিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ৩৪ লাখ ১৭ হাজার টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। অর্থাৎ দুই সংস্থার উৎপাদনের তথ্যে বড় ফারাক।
বাংলাদেশে বছরে মাথাপিছু পেঁয়াজের ব্যবহার ১৫ কিলোগ্রাম (ভারতে ১৬ কিলোগ্রাম)। সেই হিসাবে ১৭ কোটি মানুষের জন্য ২৫ লাখ টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। সে জায়গায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২৮ লাখ টন পেঁয়াজ প্রয়োজন বলে জানায়। সেখানে আবার ব্যবসায়ীদের দাবি, চাহিদা আরও বেশি!
এর আগে (২০২৩ এর আগে) প্রতি বছর প্রায় ৮ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু গত বছর (২০২৩) আমদানি ৯ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ উৎপাদনের দিকে যেমন সাফল্যের তথ্য দেওয়া হচ্ছে, তেমনি আমদানিও বাড়ছে। যে কারণে সঠিক ঘাটতির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।
দেখা যায়, পেঁয়াজের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। আবার জাতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বিবিএসের পরিসংখ্যান মেলে অনেক দেরিতে, তাতে অনেক কম উৎপাদনের তথ্য থাকে। আবার বিদেশি সংস্থাগুলো এসব তথ্য আমলেই নেয় না। তাদের তরফ থেকে আসে উৎপাদন চাহিদা ও আমদানির ভিন্ন তথ্য।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, ‘দেশে পেঁয়াজের যেসব তথ্য-উপাত্ত রয়েছে তাতে গরমিল আছে। এজন্য দেশের একেক মন্ত্রী একেক কথা বলেন। একেকজনের দপ্তরের তথ্য একেক রকম। সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। এটি দেশের বড় একটি সমস্যা।’
তিনি বলেন, ‘উৎপাদনের সঠিক তথ্য না থাকলে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। দুঃখজনক যে, মোটাদাগের জিনিসগুলোর তথ্যে আগে কিছুটা সামঞ্জস্য ছিল। এখন তাও নেই। প্রকৃত উৎপাদন কতটুকু হলো, কতটুকু মানুষ খেয়েছে? এ নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন তথ্য দেয়। তাহলে আমাদের সমস্যা কোথায়, আর সেটা কীভাবে সমাধান হবে তা চিহ্নিত হবে কীভাবে?’
ড. এম আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে দেশে প্রতি বছর কী পরিমাণ পেঁয়াজের প্রয়োজন, তার কত অংশ দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব এবং কত অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই।’
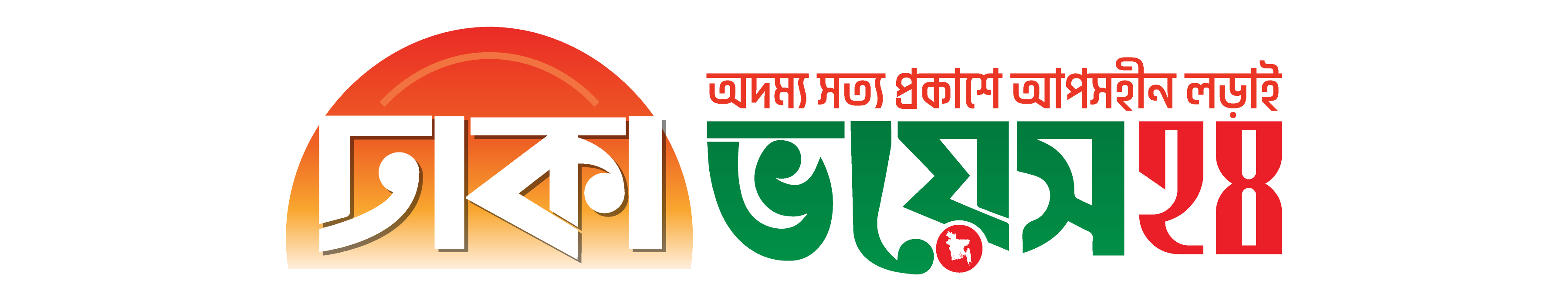

 নিজস্ব সংবাদ :
নিজস্ব সংবাদ :