ঢাকার ব্যস্ত শহরে, নামহীন মুখের ভিড়ে হারিয়ে থাকা এক মানুষ। তাঁর নাম হয়তো আপনার চেনা নয়, কিন্তু যাঁরা তাঁকে চেনেন, তাঁরা জানেন—কলেজের শিক্ষক, হল প্রভোস্ট, এমনকি কলেজ অধ্যক্ষ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখেন তাঁর হাতে। তিন দশকের এক যাত্রা—যেখানে লন্ড্রি কেবল জীবিকা নয়, হয়ে উঠেছে আত্মমর্যাদার প্রতিচ্ছবি।
তিনি শাহ আলম মামা।কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরের সিংড়া গ্রামে ১৯৯৫ সালের এক অপ্রকাশ্য ভোরে, চোখে স্বপ্ন আর কাকার হাত ধরে শাহ আলম পা রাখেন ঢাকায়। তখন বয়স ছিল ছোট, কিন্তু চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়ার বাসনা। নামে শুধু দুই শব্দ, কিন্তু ইতিহাসে এক অধ্যায়— যে ইতিহাসে আছে আইয়ুব আলী স্কুলের ধুলোমাখা খাতা, বিসিএসআইআর স্কুলের অর্ধেক রেখে যাওয়া স্বপ্ন।তবে জীবনের পাঠশালা এতটা মসৃণ ছিল না। অর্থের অভাবে থেমে যায় বইয়ের পাতা উল্টানো, থেমে যায় শ্রেণিকক্ষের স্বপ্ন। শুরু হয় জীবনের অন্য এক অধ্যায়—ঢাকায়, যেখানে বইয়ের বদলে তুলে নেন লন্ড্রী, তুলে নেন পরিবারের দায়, তুলে নেন মানবতার এক নীরব দৃষ্টান্ত।
মাত্র দুই টাকায় শুরু করেছিলেন লন্ড্রীর পথচলা—একটি জামার বিনিময়ে অল্প টাকাই ছিল তাঁর সব। সময়ের স্রোতে সেই দুই টাকা আজ ৬ হয়েছে, কিন্তু দিন শেষে আয় দাঁড়ায় কোনোমতে বেঁচে থাকার মতো। এক সময় দিনে ১০০ থেকে ১৫০ পিস জামা লন্ড্রী করে আয় হতো ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা—সেই দিন আজ শুধুই স্মৃতি। এখন তা নেমে এসেছে ৫০-৬০ পিসে, আয় কমেছে, কিন্তু ক্লান্তি বেড়েছে বহু গুণ।
করোনার কালো দিনেও এতটা ভেঙে পড়েননি শাহ আলম। বলেন, “তখনও কিছু নিয়মিত ছাত্র ছিল, তারা কাপড় দিত—বাঁচিয়ে রেখেছিল আমাকে।” কিন্তু এখন জায়গার অভাব তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। দোকানে নেই দাঁড়ানোর মতো পরিসর, নেই কাপড় রাখার জন্য ভরসাযোগ্য তাক, আর থাকার ঘর—সে তো যেন এক অন্ধ গুহা, যেখানে নেই সূর্যের আলো আসার অনুমতি , হাওয়া ঢোকে না, অথচ সেই ঘরেই বাস করেন নির্ভরতার আরেক নাম, শাহ আলম।
তবুও সেই অন্ধকার ঘরের কোণেই আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন তিনি—ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।
জীবনের একমাত্র দৃশ্যমান সাফল্য—নিজ হাতে বানানো একটি টিনশেড ঘর। কিন্তু চোখে এখনো উকি দেয় আরও বড় স্বপ্ন, আরও একটু আলো, আরেকটু ঠাঁই।
এই পেশাকে কখনোই ছোট করে দেখেননি শাহ আলম। চোখ নামিয়ে নয়, বরং বুক সোজা করে বলেন—“খারাপ লাগলেও করতে করতে মানিয়ে নিয়েছি নিজেকে।”
তাঁর হাতে যখন কাপড় যায়, সেখানে শুধু লন্ড্রী নয়, মিশে থাকে যত্ন আর নিষ্ঠার ছোঁয়া। ফরহাদ হলের সাবেক প্রভোস্ট নাসির থেকে শুরু করে কলেজের অধ্যক্ষরাও এখনো ভরসা রাখেন সেই হাতে।
শুধু পয়সার বিনিময়ে কাজ নয়, এই পেশা এক ধরনের মানবিক দায়িত্বও। অনেক শিক্ষার্থীর মানিব্যাগ ফাঁকা থাকলে তিনি ফিরিয়ে দেন না জামা, বরং বলেন, “ লন্ড্রী করে দিই, এটা আমার কর্তব্য মনে হয়।”
এ যেন লন্ড্রি নয়—এক মানুষের নিঃশব্দ নৈতিকতা, যেখানে আত্মমর্যাদা আর মানবতা পাশাপাশি হাঁটে।
ছোট এক সংসার—বাবা, মা, স্ত্রী আর একমাত্র ছেলে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি তিনি আর তাঁর জীবনের সব আলো যেন গাঁথা ছেলের চোখে।
সারাদিন কাপড়ের ভেতর ঘুরলেও মনে মনে তিনি বুনে চলেন স্বপ্ন—ছেলে একদিন বড় হবে, ভালোভাবে পড়াশোনা করবে, পাবে এক সম্মানজনক চাকরি।
নরম গলায় বলেন, “যদি সে ভালো চাকরি করে, আমি এই কাজ ছেড়ে দেব।
এ কথার মধ্যে নেই আক্ষেপ, বরং আছে এক বুক বিশ্বাস—ছেলের ভবিষ্যতে নিজের মুক্তির ঠিকানা খোঁজেন তিনি।
এ যেন এক নিঃশব্দ যোদ্ধার নীরব আকুতি, যেখানে ঘামের বিনিময়ে লেখা হয় সন্তানের আশীর্বাদের কবিতা।
সর্বস্ব উজাড় করে এই পেশাকে আঁকড়ে রেখেছেন শাহ আলম। তাঁর ছোট্ট একটিই অনুরোধ—“যদি হলের পাশে একটু জায়গা পেতাম, আয়টা হয়তো একটু বাড়ত।”
পুঁজি নেই, তাই নতুন কোনো ব্যবসার স্বপ্ন সাহস পায় না ডানা মেলতে। দিনের শুরু সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, শেষ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে—এই দীর্ঘ সময়জুড়ে চলে তাঁর নিরলস খাটুনি। শুধু জোহর আর মাগরিবের নামাজের সময়টুকুই খানিক বিশ্রাম।
শব্দে বলেন না কিছু, কিন্তু কাজের নিপুণতায় উচ্চারিত হয় আত্মসম্মানের ভাষা। প্রতিটি জামার ভাঁজে তিনি ছেপে দেন জীবনের এক অদৃশ্য ইতিহাস, যেখানে ঘামের উত্তাপে স্বপ্ন কখনও ঝলসে যায় না, বরং আরও স্পষ্ট হয় তার রেখাগুলো। শুধু কাপড়ই নয়, ধুয়ে দেন ক্লান্তি, ধুয়ে দেন অবহেলা, আর রেখে যান এক নিঃশব্দ অনুপ্রেরণা।**
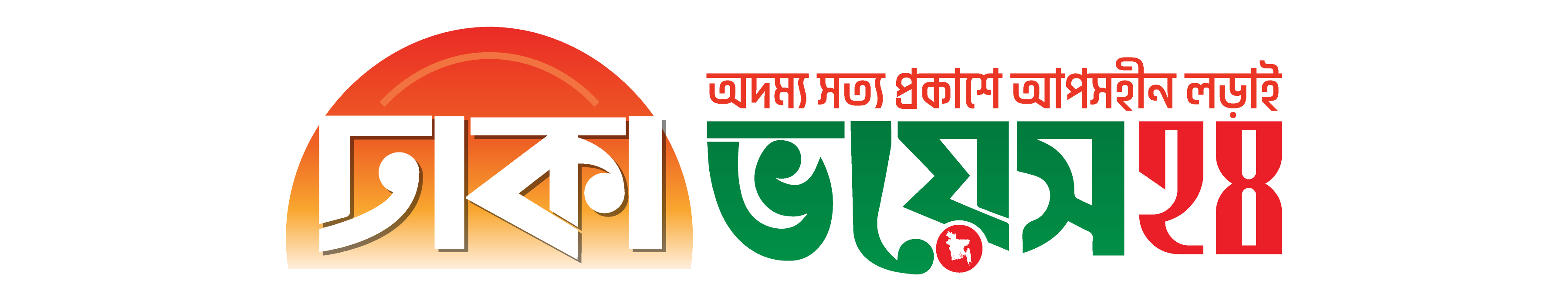

 মাহাদী হাসান
মাহাদী হাসান 

















